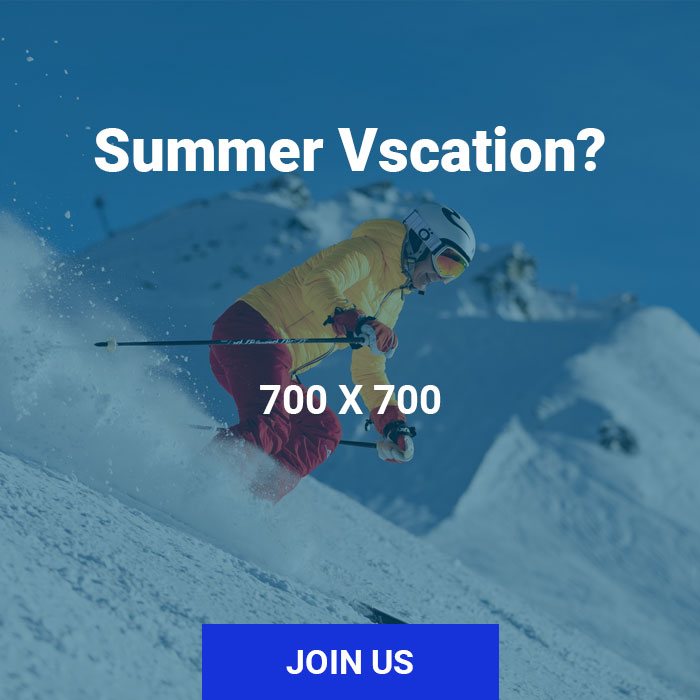আ.লীগের শক্তি জনসমর্থন-ধর্মনিরপেক্ষতা
- Jan 08 2020 01:15
১৯৪৭ সালের মধ্য-আগস্টে ভারত ও পাকিস্তান গঠিত হলে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীনতার আনন্দে উল্লসিত হয়েছিল কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা তারা পায়নি। বাঙালির প্রতিবাদ গড়ে উঠতেও দেরি হয়নি। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮-এর মার্চে ভাষার দাবিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, যার চূড়ান্ত পরিণতি বায়ান্নর রক্তঝরা ভাষা-আন্দোলন।
পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ রোজ গার্ডেনে ১৯৪৯ সালেই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা নিয়ে ‘মুসলিম’ অভিধা বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের যাত্রা শুরু ১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ভাষা আন্দোলনের বিপুল উৎসাহে ত্রিশের দশকের ধর্মভিত্তিক চিন্তাকে পরিত্যাগ করে পুনরায় ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক মঞ্চে সমবেত হয় পূর্ব বাংলার মানুষ।
বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্বে আওয়ামী লীগের মূল নেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান, জহির উদ্দিন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্বে সোহরাওয়ার্দীর পরেই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের মূল সংগঠকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতাদের বিরোধিতার মুখেও আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে শেখ মুজিবুর রহমানই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ের মূল প্রয়াস ছিল পাকিস্তানের সব গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা।
পূর্ববঙ্গের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ নিরঙ্কুশ হওয়া, নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাওয়া, রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, বিরোধ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনগণও এই ক’বছরের রাজনৈতিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের যুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণ তাদের অসহায়ত্ব তীব্রভাবে অনুভব করে। যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের নিরাপত্তা বিধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সুতরাং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন জোরালোভাবে জনগণের সামনে চলে আসে। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গড়ে তুলতে আগে থেকেই সচেষ্ট ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এ অঞ্চলের জনগণ আরো উপলব্ধি করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে কার্যত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত করে ফেলেছে।
ওই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের উদ্যোগে লাহোরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরীসহ দশ সদস্যের আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল এতে যোগদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ওই সম্মেলন ১০ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা উত্থাপন করে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। বস্তুত আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি, স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে যে চিন্তা-ভাবনা ও আন্দোলনের সূচনা করেছিল তা শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। শেখ মুজিব এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহান নেতা হিসেবে। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই সময় আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় শেখ মুজিবের ৬ দফার সামগ্রিক প্রস্তাবনা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রæয়ারি থেকে ৬ দফা আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য ও দাবিতে পরিণত হয়।
১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ আইয়ুব রাজশাহীতে প্রকাশ্যভাবে ৬ দফার সমালোচনা করলেন এবং বললেন, ইহা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা। তিনি এর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন, এই ‘জঘন্য স্বপ্ন’ বাস্তবায়ন হলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গোলামে পরিণত হবে, তাই এ কাজ তিনি কখনোই সফল হতে দেবেন না। অস্ত্রের ভাষায় ৬- দফা জবাব দেয়া হবে বলে আইয়ুব খান ঘোষণা করেন।
১৯৬৬ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইডেন হোটেলে। কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাকে দলের প্রধান মেনিফেস্টো হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকেই আওয়ামী লীগ দলের প্রধান নীতি বলে বিবেচনা করে।
১৯৬৬ সালের ১০ মে-র মধ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ৩ হাজার ৫০০ নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়ে যান। শেখ মুজিব তার আগেই সবকিছু গুছিয়ে এনেছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে কর্মীবাহিনী যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন তার সংগঠনকে। শেখ মুজিব ৬ দফার পক্ষে জেলা পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতাদেরও সংগঠিত করেছিলেন, যাতে আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুপস্থিতিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেন।
আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা ডাকা হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ১৩ মে। ছাত্রলীগের উদ্যোগই ছিল বেশি। শেখ মুজিব জেলে থেকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কাছে নির্দেশ পাঠান জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ৬ দফার পক্ষে হরতাল-মিছিল ও জনসভার কর্মসূচি নেয়ার জন্য। মাযহারুল হক বাকি, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া, শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান ও ছাত্রলীগ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে গ্রেফতার শুরু হলো কিন্তু সবাই আগে থেকেই ছিলেন সতর্ক। গ্রেফতার অভিযানে পুলিশ খুব সুবিধা করতে পারেনি। ৭ জুন, ১৯৬৬ তারিখে হরতালের পক্ষে লিফলেট ছাপিয়ে মহল্লায় মহল্লায় শুরু হয় প্রচার অভিযান। নারায়ণগঞ্জেও একই অবস্থা। ৬ জুন নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। কিন্তু দেখা গেল ৬ জুন রাত বারোটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড মিছিল হচ্ছে। হরতাল প্রতিরোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েও সরকার ব্যর্থ হলো। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সকাল থেকেই হরতাল শুরু হলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে। সকাল নয়টার দিকে তেজগাঁও শ্রমিক এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালালে বেঙ্গল বেভারেজে চাকরিরত সিলেটের অধিবাসী মনু মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। মনু মিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকসমাজ।
শ্রমিক-জনতা তেজগাঁও স্টেশনে সব ট্রেন থামিয়ে দেয়। তেজগাঁও স্টেশনের কাছে নোয়াখালীর শ্রমিক আবুল হোসেন (আজাদ এনামেল অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম কারখানা) ইপিআরের রাইফেলের সামনে বুক পেতে দেন। ইপিআর বাহিনী তার বুকেও গুলি চালায়। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত এলাকার শ্রমিক এবং আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের কর্মীরা ঢাকা শহর উত্তাল করে তোলে। নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছে পুলিশের গুলিতে ৬ শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সর্র্বস্তরের শত শত মানুষ রাজপথে নেমে আসে। পুলিশের উস্কানির মুখে জনগণ থানার মধ্যে ঢুকে যায় এবং যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার পরপরই ঢাকার শ্রমিক এলাকাগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়। গ্রেফতারের সংখ্যাও সন্ধ্যার মধ্যে দেড় হাজার ছাড়িয়ে যায়।
এরপরের ইতিহাস জেল, জুলুম, হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টার ইতিহাস। যার চূড়ান্ত রূপ ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’। কিন্তু ’৬৯-এর অভ‚তপূর্ব গণ-আন্দোলন সব অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয়। গণ-অভ্যুত্থানে পতন ঘটে আইয়ুব শাহীর এবং শেখ মুজিবুর রহমান রূপান্তরিত হন বাঙালির প্রিয় নেতা ‘বঙ্গবন্ধু’তে।
সব রকম নির্যাতন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ৩০ লাখ শহীদ আর দুই লাখ মা-বোনের অমূল্য সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো নিজস্ব নিয়মনীতি ছিল না, হয় ব্রিটিশ নয়তো পাকিস্তান এই দুই নীতিতেই চলেছে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ মাত্র ১০ মাসে সংবিধান রচনা করে বাংলাদেশকে একটি সুন্দর শব্দ উপহার দেন, যার নাম ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’।
বাংলাদেশের মানুষ চিরদিনই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙালির এই গভীর অনুভবের জায়গাটি অনুধাবন করতে পেরে ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে জাতীয় চার নীতি (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ) অন্তর্ভুক্ত করেন তাদের মধ্যে স্থান দেন ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মানুষ যেই কাজটি অত্যন্ত উৎসাহিত মনে, স্বেচ্ছায় করতে পেরেছিলেন তা আজ করে দেখানো বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত কঠিন।
একটি রাষ্ট্র যখন গঠিত হয়, তখন সেখানে নানা সম্প্রদায়ের লোক এসে ভিড় জমায়। এই নানা সম্প্রদায়ের ভাব-ভাষা-সংস্কৃতিও হয় নানা রকমের আর এই জন্যই পৃথিবীর প্রায় রাষ্ট্রেই দেখা যায় বর্ণিল সংস্কৃতি। এই বহুবর্ণতাই রাষ্ট্রের প্রাণ। ওই বহুবর্ণতা চাই বলেই আমরা ক্রসেড কিংবা জিহাদ চাই না, আল কায়েদা কিংবা বোকো হারাম চাই না, চাই না তালেবান কিংবা আইএস-আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের মতো ভয়ঙ্কর জঙ্গি সংগঠন। ধর্মনিরপেক্ষতা এই বহুবর্ণ সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা ভৌগোলিক ঐক্য টিকিয়ে রাখে। এ কথাটি রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন বলেই সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ সন্নিবেশিত করেন। বাংলাদেশ এগিয়ে চলে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ‘ধর্মে উদাসীন’ রাষ্ট্রের মুকুট মাথায় নিয়ে। দেশ তখন ভালোই চলছিল। দেশে আর যাই থাকুক কিন্তু কোনো ধর্মীয় সন্ত্রাস ছিল না, ওই পরিস্থিতিতে যা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কারণ তখন কম-বেশি সবার হাতেই অস্ত্র ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সবাই ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলে বাঙালি জাতির ঐক্য তৈরি করে।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সবকিছু তছনছ করে দেয়। দেশ চলে যায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা জেনারেল বা স্বঘোষিত জেনারেলদের বুটের তলায়। যেমনটি হয়েছিল আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার আমলে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে একাত্তরের পরাজিত শক্তি গোপনে গোপনে সুযোগ খুঁজতে থাকে, তাদের এই সুযোগকে বাস্তবায়ন করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জেনারেল জিয়া বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের ক্ষমতার ভাগ দেন এবং সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যাওয়ার প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট।
মানুষের ‘ধর্মবিশ্বাস’ থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো ‘ধর্ম’ থাকে না। থাকা উচিতও নয়। কারণ সব ধর্মের লোকই রাষ্ট্রে বসবাস করে। কোনো ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দিলে রাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হীনতা বোধ করেন এবং বঞ্চিত হন। তাই উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় সেসব রাষ্ট্রের ‘রাষ্ট্রধর্ম’ বলে কিছুই নেই।
১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক ও আধুনিক সংবিধান। ওই সংবিধানে জেনে বুঝেই বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ-রাষ্ট্র বলা হয়েছিল কিন্তু ১৯৭৫-পরবর্তী কালপর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর কেটে-ছিঁড়ে বিকলাঙ্গ করা হয় বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান। তাতে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ও স্বৈরাচারী এরশাদ যুক্ত করেন ‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘রাষ্ট্রধর্ম’। এটা তারা ধর্মকে ভালোবেসে করেননি, করেছিলেন ধর্মকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে।
জিয়া ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে আদেশ বলে সংবিধানের প্রস্তাবনার আগে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ যুক্ত করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ স্থাপন করেন। তিনি সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ উচ্ছেদ করেন। এই ১২ অনুচ্ছেদ উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নতুন করে আমদানি হয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল ও তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর জেনারেল এইচ এম এরশাদ এসে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের ‘রাষ্ট্রধর্ম’ ঘোষণা করে।
বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতের ফলে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়, সম্প্রীতি বিঘিœত হয়, বাংলাদেশে তাই হয়েছে। দীর্ঘ একুশ বছর (’৭৫ থেকে ’৯৬ পর্যন্ত) বাংলাদেশে তথাকথিত ইসলামপন্থিদের সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের মগজ এমনভাবে ধোলাই করা হয় যেন বাংলাদেশ আর ইসলাম সমার্থক, যে কথা পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানি চাটুকারেরা বলত। দেশের সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য সব জেলায় একসঙ্গে বোমা ফাটানোর ঘটনা ঘটে। জেএমবি, হিযবুত তাহরীর, আনসারউল্লাহ বাংলা টিম, হরক-উল- জিহাদসহ মুফতি হান্নানগং- কাদের সৃষ্টি, কার স্বার্থে সৃষ্টি এসব আজ দেশের মানুষ বুঝতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা। এদের নির্মূল করে আবার আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় যেতে হবে। সেখানে যেতে না পারলে আমাদের পরাজয় ঘটবে।
মুজিব বর্ষে আওয়ামী লীগকে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি মানুষের ‘মাইন্ডসেট’ একাত্তরের মতো পরিবর্তন করতে পারি তাহলে এই কাজটি খুব সহজেই করা সম্ভব। আমরা আর সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা চাই না, যেটা এখন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে সংঘটিত হচ্ছে। যদি আমরা এই রকম অমানবিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলার মাটিতে না চাই, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব আবার আমাদের গণঐক্যের বন্ধনে ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে গেলেই তৈরি করা সম্ভব হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।
লেখক: মোনায়েম সরকার - রাজনৈতিক বিশ্লেষক
মানবকণ্ঠ/টিএইচডি
আরো সংবাদ
রামাপালে বেপরোয়া ট্রাক চাপায় প্রাণ গেল ৩ জনের
- Jan 08 2020 01:15
কালিগঞ্জে বিষাক্ত কেমিকেল দিয়ে পাকানো আম জব্দ ও বিনষ্ট
- Jan 08 2020 01:15
সৈয়দপুরে সাংবাদিকদের কটুক্তি ও মামলার হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন
- Jan 08 2020 01:15
সর্বশেষ
Weather

- London, UK
 13%
13% 6.44 MPH
6.44 MPH
-
 23° Sun, 3 July
23° Sun, 3 July -
 26° Sun, 3 July
26° Sun, 3 July